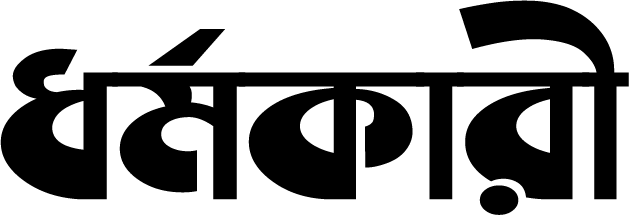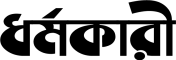“পথিক, তুমি কি পথ হারাইয়াছ?” – কপালকুন্ডলা উপন্যাসের এই জনপ্রিয় প্রশ্নটিকে চিরায়ত দর্শনের প্রেক্ষিতে এভাবেও করা যায়: এমন কোন পথিক কি আছে যে একটিবারের জন্যও পথ হারায়নি? পথ চলতে গিয়ে আমরা পথ হারাই, পথ খুঁজেও পাই। কিন্তু প্রশ্ন হলো – আমরা কীভাবে পথ চিনি? পরিচিত জায়গায় গেলে কীভাবে বুঝি যে ওখানে আমরা আগেও এসেছিলাম? কিংবা একেবারে নতুন পরিবেশে গেলে কীভাবে বুঝি যে পরিবেশটা নতুন? পরিবেশের জটিল স্মৃতি আমরা কীভাবে ধরে রাখি?
এসব প্রশ্নের মোটামুটিভাবে যে উত্তর আমরা সবাই জানি তা হলো আমাদের মগজের মেমোরি সেল বা স্মৃতিকোষে জমা থাকে এসব তথ্য। আমরা যখন নতুন কিছু দেখি আমাদের মস্তিষ্ক নতুন তথ্যগুলি ধারণ করে স্মৃতিকোষে জমা রাখে। আমরা এটাও জানি যে বিভিন্ন প্রাণির স্মৃতিধারণ ক্ষমতা বিভিন্ন – যেমন হাতির স্মৃতিশক্তি খুব প্রখর, কিন্তু গোল্ডফিশের স্মৃতিশক্তি প্রায় নগণ্য। মানুষেরও মস্তিষ্কের স্মৃতিধারণ ক্ষমতা সবার সমান নয়। বয়স, অনুশীলন এবং অভিজ্ঞতা বাড়ার সাথে সাথে স্মৃতিধারণ ক্ষমতাও তুলনামূলকভাবে বেড়ে যায়। যে পথ আমরা ছোটবেলায় কিছুতেই চিনতে পারতাম না, বড় হয়ে সেই পথ চিনতে আমাদের সমস্যা হয় না।
একটু ভাবলেই বুঝতে পারবো – কীভাবে আমরা কোন রাস্তা বা স্থান বা পরিবেশ চিনতে পারি বা মনে রাখি। একটা ঘটনার মাধ্যমে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করা যাক। বেশ কয়েক বছর পরে মেলবোর্ন থেকে ঢাকায় গিয়েছি। ভাগনির বাসার ঠিকানা জানা আছে, কিন্তু বাসা চিনি না। ঢাকা শহরে ঠিকানা ধরে বাসা খুঁজে বের করা যে সহজ নয় তা আমরা জানি। তাই যখন বাসা খুঁজতে যাই – আমাদের মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষগুলো খুবই উদ্দীপ্ত হয়। আমরা মনে রাখার চেষ্টা করি কোন্ রাস্তার পর কোন্ দিকে মোড়, কোন্ বিল্ডিং বা কোন্ বাজার অর্থাৎ অনেকেই চেনে এরকম স্থায়ী কোন পয়েন্ট। আমার ক্ষেত্রে ভাগনি বলে দিয়েছে তাদের বাসা হাতির পুল বাজারের কাছে, মোতালেব প্লাজার পেছনে। সিএনজি ট্যাক্সিওয়ালা হাতিরপুল বাজারে নিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে আমার মস্তিষ্ক দ্রুত চারদিকের পরিবেশ স্ক্যান করতে শুরু করলো মোতালেব প্লাজার খোঁজে। ওটা খুঁজে পাবার পরের পয়েন্ট হলো তার পেছনের দিক কোন্টা বের করা। এভাবে একের পর এক সিকোয়েন্স, দূরত্ব, সময়, অবস্থান ইত্যাদি মিলিয়ে আমরা বাসা খোঁজার পুরো এপিসোডটা মনে রাখি। একবার চিনে ফেলার পর দ্বিতীয়বার কিন্তু ব্যাপারটা সহজ হয়ে যায়। কারণ পরিচিত পরিবেশ দেখলেই মস্তিষ্কের স্মৃতিকোষ উদ্দীপ্ত হয়।
এখন মনে করুন, আরো অনেক বছর কেটে গেলো। ঢাকা শহরে ব্যাপক পরিবর্তন হলো। হাতিরপুল বাজার উঠে গেলো। মোতালেব প্লাজার নাম পরিবর্তন হয়ে গেলো, বিল্ডিং-টার চেহারাই পাল্টে গেলো। অর্থাৎ পুরো পরিবেশটাই নতুন হয়ে গেলো। আমার মস্তিষ্ক কিন্তু তখন ঐ জায়গায় গেলে সমস্যায় পড়ে যাবে। ঠিক চিনতে পারবে না জায়গাটা। কারণ মগজে যে স্মৃতি রাখা আছে তার সাথে নতুন পরিবেশের মিল নেই। মস্তিষ্ক আবার নতুন করে নতুন পরিবেশের স্মৃতি ধারণ করবে। কিন্তু চোখের সামনে যদি পরিবেশ বদলাতে থাকে – অর্থাৎ আমরা যদি তা দেখতে থাকি – আমাদের মস্তিষ্কের স্মৃতিকোষে সেই তথ্য জমা থাকে। তখন আমাদের কাছে ব্যাপারটা ততটা নতুন বলে মনে হয় না।
পথ ও অবস্থান খুঁজে বের করার জন্য এখন কত ধরনের যান্ত্রিক ব্যবস্থা আছে। গ্লোবাল পজিশানিং সিস্টেম বা জি-পি-এস এখন সুলভ এবং বহুল ব্যবহৃত একটি পদ্ধতি। গাড়ি চালানোর ক্ষেত্রে এখন জি-পি-এস বিশেষ পথ-প্রদর্শকের কাজ করে। উপগ্রহের মাধ্যমে আমরা আমাদের অবস্থান এবং গন্তব্যের দিক-নির্দেশনা পাই জি-পি-এসের সাহায্যে। কিন্তু সেখানেও যদি ম্যাপ আপডেট করা না থাকে তাহলে মাঝে মাঝে বিপদে পড়তে হয়।
মানুষের ক্ষেত্রে পথ খুঁজে বের করার পদ্ধতি সম্পর্কে একটা ভাসা ভাসা ধারণা পাওয়া গেলো। ভাসা ভাসা বললাম এই কারণে যে মস্তিষ্কের সবগুলো কোষের কার্যপদ্ধতি নিশ্চিন্তভাবে জানা যায়নি এখনো। আমরা এখনো জানি না ঠিক কী কারণে আলজেইমার্স জাতীয় রোগ হয়, বা স্মৃতি-বিনাশ ঘটে। বিজ্ঞানীরা এটুকু নিশ্চিতভাবে জানতে পেরেছেন যে আলজেইমার্স রোগীর হিপোক্যাম্পাস ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মানুষের রোগের কারণ সম্পর্কিত গবেষণার জন্য বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বিজ্ঞানীদের নির্ভর করতে হয় ইঁদুর বা অন্যন্য প্রাণী নিয়ে গবেষণালব্ধ ফলের ওপর। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে ইঁদুর বা অন্যান্য প্রাণিরা পথ বা পরিবেশ কীভাবে চেনে বা মনে রাখে? সব প্রাণির মগজেই কি আছে কোন না কোন ধরনের জি-পি-এস? এ সংক্রান্ত ব্যাপক গবেষণা করে যুগান্তকারী আবিষ্কার করেছেন আমেরিকান-ব্রিটিশ বিজ্ঞানী জন ও’কিফ এবং নরওয়ের বিজ্ঞানী দম্পতি মে-ব্রিট মোজার ও এডভার্ড মোজার। আর তাই ২০১৪ সালে চিকিৎসাবিজ্ঞানে (ফিজিওলজি অর মেডিসিনে) নোবেল পুরষ্কার অর্জন করেছেন এই তিনজন বিজ্ঞানী।
যেভাবে শুরু
আমেরিকান মনোবিজ্ঞানী এডোয়ার্ড টলম্যান ১৯৪৮ সালে ফিজিওলজিক্যাল রিভিউতে প্রকাশিত তাঁর ‘কগনিটিভ ম্যাপ্স ইন র্যাফট্স অ্যান্ড ম্যান’ শিরোনামের গবেষণাপত্রে [১] প্রাণী কীভাবে পথ চেনে তার একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেন। তিনি দেখান যে প্রাণিরা স্থান ও ঘটনার সমন্বয় ঘটিয়ে পরিবেশের চিত্র মনে রাখতে পারে। ক্রমঘটমান ঘটনা ও ক্রম-অগ্রসরমান অবস্থানের সমন্বয়ে প্রাণির মগজের মধ্যে ক্রমান্বয়ে একটা সামগ্রিক মানসিক ম্যাপ তৈরি হয়। ওই মানসিক ম্যাপ দেখেই প্রাণিরা পথ চেনে। টলম্যানের তত্ত্ব পথ চেনার প্রক্রিয়া সম্পর্কে একটা বৈজ্ঞানিক ধারণা দেয় ঠিকই, কিন্তু মগজের ঠিক কোন্ জায়গায় এবং ঠিক কী প্রক্রিয়ায় এই মানসিক ম্যাপ তৈরি হয় সে সম্পর্কে কোন ধারণা দেয় না।
পরবর্তী বিশ বছর ধরে অনেক বিজ্ঞানীই অনেক রকমের গবেষণা করেছেন এ ব্যাপারে। কিন্তু ১৯৭১ সাল পর্যন্ত তেমন সুনির্দিষ্ট কোন সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব হয়নি। ১৯৭১ সালে বিজ্ঞানী জন ও’কিফ প্রাণির মস্তিষ্কে প্লেইস সেল বা স্থানিক কোষ আবিষ্কার করে প্রাণির পথ চেনার পদ্ধতি সম্পর্কিত গবেষণায় নতুন পথের সন্ধান দেন।
জন ও’কিফ এবং প্লেইস সেল
জন মাইকেল ও’কিফের জন্ম ১৯৩৯ সালের ১৮ নভেম্বর, নিউইয়র্ক শহরে। তাঁর মা-বাবা ছিলেন আইরিশ ইমিগ্র্যান্ট। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের শুরুতে স্নায়ুকোষ নিয়ে গবেষণা করবেন এরকম কোন ইচ্ছে ছিলো না জন ও’কিফের। নিউইয়র্ক ইউনিভার্সিটি থেকে অ্যারোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করার পর তাঁর ইচ্ছে হলো মনের দর্শন (ফিলোসফি অব দি মাইন্ড) সম্পর্কে পড়াশোনা করার। ১৯৬০ সালে ভর্তি হয়ে গেলেন নিউইয়র্ক সিটি কলেজে। ১৯৬৩ সালে সাইকোলজিতে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন জন। তারপর চলে যান কানাডায়। ফিজিওলজিক্যাল সাইকোলজি (শারীরতাত্ত্বিক মনোবিজ্ঞান) বিষয়ে মন্ট্রিয়েলের ম্যাকগিল ইউনিভার্সিটি থেকে পিএইচডি করেন অধ্যাপক রোনাল্ড মেলজ্যাকের তত্ত্বাবধানে। তাঁর পিএইচডি গবেষণার বিষয় ছিল ‘সেন্সরি প্রপার্টিজ অব অ্যামিগডালা’। প্রাণির ঘ্রাণ নেবার ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করে অ্যামিগডালার কোষগুলো।
পিএইচডি করার পর ১৯৬৭ সালে ইউ এস ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব মেন্টাল হেল্থ এর পোস্টডক্টরাল ফেলো হিসেবে যোগ দেন ইউনিভার্সিটি কলেজ অব লন্ডনে। নিউইয়র্ক সিটি কলেজের দর্শন ক্লাসে পরিচয় হয়েছিল ইলিনের সাথে। তারপর প্রেম। ছয় বছর প্রেমের পর ১৯৬৭তে বিয়ে করেন ইলিনকে। ইলিন ইতোমধ্যে পিএইচডি করেছেন। নতুন চাকরি আর নতুন বউ নিয়ে জন চলে এলেন লন্ডনে। তারপর আর পুরোপুরি ফিরে যাওয়া হয়নি আমেরিকায়। ব্রিটিশ নাগরিকত্ব নিয়ে থেকে গেছেন লন্ডনে।
শুরুতে অ্যামিগডালার কোষ নিয়ে গবেষণা করলেও লন্ডনে এসে তাঁর গবেষণার ক্ষেত্র প্রসারিত হয় হিপোক্যাম্পাসে। ও’কিফ হিপোক্যাম্পাসের ভূমিকা নিয়ে আগ্রহী হন। প্রাণির জীবনে হিপোক্যাম্পাসের ভূমিকা কী? প্রাণির স্মৃতি সংরক্ষণে মস্তিষ্কের হিপোক্যাম্পাসের একটা ভূমিকা আছে তা জানা গেছে ১৯৫৭ সালে। হেনরি মোলেইসন নামে এক রোগীর মৃগীরোগ সারানোর জন্য দুটো হিপোক্যাম্পাসই কেটে বাদ দেয়ার পর দেখা গেছে যে হেনরি তাঁর স্মৃতিশক্তির অনেকখানিই হারিয়েছেন।
হিপোক্যাম্পাসের সুনির্দিষ্ট ভূমিকার ব্যাপারটা কিন্তু প্রতিষ্ঠিত হয়নি তখনো। ইঁদুরের হিপোক্যাম্পাস নিয়ে গবেষণা শুরু করেন ও’কিফ। ইঁদুরের হিপোক্যাম্পাসের পরিবর্তন ঘটিয়ে (আস্তে আস্তে কিছুটা করে কেটে নিয়ে) তিনি ইঁদুরের ব্যবহার পর্যবেক্ষণ করেন। তিনি দেখেন হিপোক্যাম্পাসের ক্ষতি হলে ইঁদুর আর জায়গা চিনতে পারছে না। নতুন জায়গায় গেলে ইঁদুরের যে উত্তেজনা বাড়ে তা হিপোক্যাম্পাসের অনুপস্থিতিতে কমে যায়। অনেক পরীক্ষা করে ও’কিফ দেখেন যে হিপোক্যাম্পাসের কিছু কোষ শুধুমাত্র প্লেইস বা জায়গার পরিবর্তন হলে উত্তেজিত হয়। তিনি এই কোষগুলির নাম দিলেন ‘প্লেইস সেল’। প্লেইস সেলগুলো শুধুমাত্র জায়গা পরিবর্তন বা দিক পরিবর্তনের সময় উত্তেজিত হয়। ১৯৭১ সালে তিনি তাঁর ছাত্র জনাথন ডস্ট্রভিস্কির সাথে প্লেইস সেলের ফলাফল প্রকাশ করেন [২]। তাঁর পেপার থেকে আমরা জানতে পারি হিপোক্যাম্পাস ক্ষতিগ্রস্ত হলে প্রাণী জায়গা চিনতে পারে না, পথ ভুলে যায়।
প্লেইস সেলগুলোর উত্তেজনা জন ও’কিফের আগে আর কেউ পর্যবেক্ষণ করেননি। ও’কিফ আবিষ্কার করলেন যে প্লেইস সেলগুলো শুধুমাত্র পরিচিত পরিবেশে পেলেই উদ্দিপ্ত হচ্ছে, বিভিন্ন প্লেইস সেল মিলে পরিবেশ সম্পর্কে একটা সুনির্দিষ্ট ছক তৈরি হচ্ছে মস্তিষ্কের হিপোক্যাম্পাসে। তিনি আরো দেখালেন যে হিপোক্যাম্পাসে বিভিন প্লেইস সেলের সমন্বয়ে বিভিন্ন পরিবেশের অসংখ্য মানসিক ম্যাপ সংরক্ষিত থাকতে পারে।
১৯৭৮ সালে লিন ন্যাডেলের সাথে তিনি প্রকাশ করেন তাঁর ক্লাসিক বই ‘হিপোক্যাম্পাস অ্যাজ এ কগনিটিভ ম্যাপ’ [৩]। এই বইতে তিনি বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করেন কীভাবে হিপোক্যাম্পাসে প্লেইস সেলগুলো স্থানিক স্মৃতি ধরে রাখে। তাঁর তত্ত্ব আমাদের স্থান-কাল ও ঘটনা মনে রাখার পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা দেয়। অনেক সময় দেখা যায় – যেসব ঘটনা আমরা এমনিতে মনে রাখিনা – কোন একটা জায়গায় গেলে সেসব ঘটনাও মনে পড়ে। এসব স্মৃতিকে আমরা ‘এপিসোডিক মেমোরি’ বলতে পারি।
জন ও’কিফের আবিষ্কার স্নায়ুবিজ্ঞানের গবেষণায় ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। সারা পৃথিবীতে অসংখ্য বিজ্ঞানী প্লেইস সেল সংক্রান্ত তত্ত্বীয় ও পরীক্ষামূলক গবেষণায় লিপ্ত হন। এসব গবেষণার ফল থেকে প্রতিষ্ঠিত হয় যে প্লেইস সেলগুলো মগজে স্থানিক পরিবেশের একটা ম্যাপ তৈরি করে তা স্মৃতিতে সংরক্ষণ করে। স্মৃতি সংরক্ষণে হিপোক্যাম্পাসের ভূমিকা মানুষের মানসিক রোগের কারণ ও চিকিৎসা সংক্রান্ত গবেষণায় নতুন পথের সন্ধান দেয়। আলজেইমার্স রোগীদের মস্তিষ্কের এম-আর-আই স্ক্যান পরীক্ষা করে দেখা গেছে তাদের হিপোক্যাম্পাস ক্ষতিগ্রস্ত। গবেষণা চলতে থাকে।
১৯৮৭ সালে প্রফেসর হয়েছেন জন ও’কিফ। পেয়েছেন রয়েল সোসাইটি ও একাডেমি অব মেডিকেল সায়েন্সের সদস্যপদ। ২০০১ সালে পেয়েছেন ফেল্ডবার্গ ফাউন্ডেশান প্রাইজ, ২০০৭ সালে গ্রোয়েমেয়ার প্রাইজ ফর সাইকোলজি, ২০০৮ সালে ব্রিটিশ নিউরোসায়েন্স অ্যাওয়ার্ড।
তাঁর স্ত্রী ইলিন ও’কিফ লন্ডন মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটির পাবলিক হেল্থের প্রফেসর হিসেবে অবসর নিয়েছেন ২০১১ সালে। জন ও ইলিন ও’কিফের দুই ছেলে কিরন ও রাইলি। গবেষণা ছাড়া আরো দুটো কাজ খুব উৎসাহ নিয়ে করেন জন ও’কিফ – বাস্কেট বল খেলা ও ইলিনের সাথে দক্ষিণ ইংল্যান্ডের পাহাড়ে ও সৈকতে ঘুরে বেড়ানো।
২০১৪ সালে জন ও’কিফের সাথে চিকিৎসাবিজ্ঞানে আরো যে দু’জন নোবেল পুরষ্কার পেয়েছেন তাঁরা হলেন মে-ব্রিট মোজার ও এডভার্ড মোজার। তাঁরা দু’জনের মূল গবেষণা কিন্তু শুরু হয়েছিল জন ও’কিফের ল্যাবোরেটরিতে তাঁরই তত্ত্বাবধানে। এবার আসছি তাদের কথায়।
মে-ব্রিট মোজার ও এডভার্ড মোজার এবং গ্রিড সেল
মে-ব্রিট ও এডভার্ড মোজার দম্পতি হলেন নোবেল পুরষ্কার প্রাপ্ত পঞ্চম দম্পতি। নরওয়ের মে-ব্রিট ও এডভার্ড যুগলকে ‘দুই শরীরে এক মস্তিষ্ক’ বলেই জানে সবাই। কারণ তাঁদের কাজ এতটাই ছন্দোবদ্ধ।
নরওয়ের একেবারে পশ্চিম সীমান্তের একটি প্রত্যন্ত দ্বীপাঞ্চলে জন্ম দু’জনেরই – অবশ্য ভিন্ন ভিন্ন দ্বীপে। এডভার্ডের জন্ম ১৯৬২ সালের ২৭ এপ্রিল, মে-ব্রিটের জন্ম ১৯৬৩ সালের ৪ জানুয়ারি। তাঁদের কারোরই মা-বাবা উচ্চশিক্ষার সুযোগ পাননি। তাই সন্তানের উচ্চশিক্ষার ব্যাপারে তাঁদের উৎসাহের অন্ত ছিল না। ১৯৮৩ সালে অসলো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার পর সাইকোলজি ক্লাসে পরিচয় হলো মে-ব্রিট ও এডভার্ডের। তারপর কিছুদিনের মধ্যেই মন-বিনিময়। ক্রমশ তাঁরা বুঝতে পারলেন স্নায়ুকোষের কার্যকলাপের ওপর প্রাণির আচার আচরণের নির্ভরশীলতা সম্পর্কে জানার আগ্রহ তাঁদের প্রবল।
কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন নিউরো-সায়েন্সের কোন কোর্স নেই। তাঁদের আগ্রহ দেখে আন্ডারগ্র্যাজুয়েট কোর্সের বিহেভিয়ার অ্যানালাইসিসের শিক্ষক কার্ল এরিক গ্রিনেচ ১৯৭৯ সালে প্রকাশিত সায়েন্টিফিক আমেরিকানের ‘ব্রেইন’ সম্পর্কিত একটা বিশেষ সংখ্যা পড়তে দেন। তাঁরা যেন হাতে চাঁদ পেলেন। ঐ বিশেষ সংখ্যায় তখনকার সময়ের অনেক বিখ্যাত স্নায়ুবিজ্ঞানীর লেখা ছিল – যা পড়ে খুবই উদ্দীপ্ত হলেন এডভার্ড ও মে-ব্রিট। স্নায়ুবিজ্ঞানে গবেষণা করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠলেন তাঁরা।
অসলো ইউনিভার্সিটিতে তখন একজন মাত্র গবেষক মনোবিজ্ঞানী ছিলেন যিনি নিউরোসায়েন্স নিয়ে গবেষণা করছিলেন। তাঁর নাম টেরজি স্যাগভোল্ডেন। মে-ব্রিট ও এডভার্ড মনোবিজ্ঞানের পড়াশোনার পাশাপাশি দু’বছর ধরে কঠোর পরিশ্রম করলেন স্যাগভোল্ডেনের তত্ত্বাবধানে স্নায়ুবিজ্ঞানের গবেষণায়। প্রাণির আচরণ ও প্রাণী নিয়ে গবেষণা-পরীক্ষণের খুঁটিনাটি শিখলেন একেবারে গোড়া থেকে।
মে-ব্রিট ও এভডার্ড মন ও কাজের দিক থেকে পরস্পর এতটাই এক হয়ে গেলেন যে তাঁরা সেটাকে চিরস্থায়ী রূপ দিতে দেরি করলেন না। ১৯৮৪ সালে আন্ডারগ্র্যাজুয়েটে থাকতেই তাঁরা তানজানিয়ার মাউন্ড কিলিম্যাঞ্জারোর ডরম্যান্ট ভলকানোর চূড়ায় উঠে আংটি বিনিময় করেন। যুগল-জীবনের বড় বড় সিদ্ধান্তগুলো দ্রুত নিয়ে নিলেন তাঁরা। সিদ্ধান্ত নিলেন – যত দ্রুত সম্ভব দুটো সন্তানের মা-বাবা হবেন। ডক্টরেট করার পর পোস্ট-ডক্টরেট করবেন দেশের বাইরে। তারপর দু’জনে মিলে একটা গবেষণাগার গড়ে তুলবেন যেখানে কাটবে তাঁদের সারাজীবন। গবেষণাগারটি পৃথিবীর যে-কোন জায়গায় হতে পারে।
স্নাতক ডিগ্রি করার পর মে-ব্রিট ও এডভার্ড গেলেন নরওয়ের সবচেয়ে বিখ্যাত ইলেকট্রো-ফিজিওলজিস্ট পার অ্যান্ডারসনের কাছে তাঁর অধীনে আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রজেক্ট করার আবেদন নিয়ে। পার অ্যান্ডারসন তখন হিপোক্যাম্পাসে নিউরনের অ্যাক্টিভিটি সংক্রান্ত গবেষণা করছেন। তিনি যদিও শুরুতে জন ও’কিফের প্লেইস সেলের সাথে একমত হতে পারেননি, কিন্তু হিপোক্যাম্পাসের কোষগুলো যে প্রাণির পরিবেশ চেনায় ভূমিকা রাখে তাতে কোন সন্দেহ ছিল না তাঁর। অ্যান্ডারসন শুরুতে রাজি ছিলেন না মোজারদের সুপারভাইজার হতে। কিন্তু মে-ব্রিট ও এডভার্ড নাছোড়বান্দা। অ্যান্ডারসন শেষপর্যন্ত একটা প্রজেক্ট দিলেন তাদের। কাজ শুরু করলেন মে-ব্রিট ও এডভার্ড। তাদের প্রথম কাজ হলো ইঁদুরের হিপোক্যাম্পাস একটু একটু করে কেটে ফেলে দিয়ে ইঁদুরের আচরণের কী কী পরিবর্তন হয় তা পর্যবেক্ষণ করা। এভাবে ঠিক কতটুকু হিপোক্যাম্পাস কেটে ফেলে দিলে ইঁদুর আর নতুন পরিবেশ চিনতে পারবে না বের করলেন মে-ব্রিট ও এডভার্ড।
তখনো পর্যন্ত ধারণা ছিল যে পরিবেশ চেনার ব্যাপারে মস্তিষ্কের হিপোক্যাম্পাসের সামনের দিক ও পেছনের দিন সমান ভূমিকা রাখে। কিন্তু প্রফেসর অ্যা ন্ডারসনের অধীনে কাজ করতে গিয়ে মে-ব্রিট ও এডভার্ড আবিষ্কার করলেন যে হিপোক্যাম্পাসের সামনের দিকের চেয়ে পেছনের দিকটা বেশি ভূমিকা রাখছে ইঁদুরের পরিবেশ চেনার ক্ষেত্রে। এই আবিষ্কার তাঁদের পরবর্তী গবেষণায় ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে।
আন্ডারগ্র্যাজুয়েট শেষ করে প্রফেসর অ্যান্ডারসনের অধীনে পিএইচডি করলেন মে-ব্রিট ও মোজার। মগজের স্মৃতিধারণে হিপোক্যাম্পাল সেলের ভূমিকা নিয়ে গবেষণা করে তাঁরা একই সাথে পিএইচডি ডিগ্রি পেলেন ১৯৯৫ সালে। পিএইচডি গবেষণাকালে প্রফেসর অ্যান্ডারসনের মাধ্যমে মোজারদের সাথে পরিচয় হয় এডিনবরা ইউনিভার্সিটির প্রফেসর রিচার্ড মরিস ও ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডনের প্রফেসর জন ও’কিফের সাথে। সেদিন অবশ্য মোজাররা স্বপ্নেও ভাবেননি যে একদিন তাঁরা জন ও’কিফের সাথে নোবেল পুরষ্কারের অংশীদার হবেন।
পিএইচডি করার পর মে-ব্রিট ও এডভার্ড পোস্টডক্টরাল গবেষণা করার সুযোগ পেলেন জন ও’কিফের ল্যাবে। সেখানে তাঁরা শিখলেন হিপোক্যাম্পাসের প্লেস সেল রেকর্ডিং সিস্টেম। এক প্রবন্ধে মোজাররা স্বীকার করেছেন যে জন ও’কিফের ল্যাবে তাঁরা কয়েক মাস কাজ করে যা শিখেছেন তা অন্য সব শিক্ষার চেয়েও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ [৪]।
কয়েক মাস পর তাঁদের নিজেদের ল্যাবোরেটরি গড়ার স্বপ্ন হঠাৎ সার্থক হয়ে গেলো। ১৯৯৬ সালের আগস্ট মাসে মোজাররা তাঁদের নিজেদের দেশ নরওয়ে থেকে একটা চমৎকার অফার পেলেন। নরওয়েজিয়ান ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি তাঁদের দু’জনের জন্যই দুটো অ্যাসোসিয়েট প্রফেসরের পদ সৃষ্টি করেছেন। ইতোমধ্যে তাঁদের পরিকল্পনা অনুযায়ী তাঁরা দুই সন্তানের জনক-জননী হয়েছেন। দেশের বাইরে পোস্টডক্টরেট গবেষণার অভিজ্ঞতাও হয়েছে। এখন নিজেদের ল্যাব গড়ার সুযোগ এসেছে নিজেদের দেশেই। এরকম সুযোগ সহজে আসে না। হোক না তা নরওয়ের ছোট্ট একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে।
দ্রুত কাজে লেগে গেলেন মোজার দম্পতি। একেবারে গোড়া থেকে শুরু করলেন পরীক্ষাগার তৈরি করার কাজ। ইউনিভার্সিটির একটা বিল্ডিং-এর বেসমেন্টের কয়েকটা ঘর নিয়ে তৈরি হলো ল্যাব। শুরুতে বায়োলজিক্যাল রিসার্চের সবচেয়ে জরুরি অংশ – ‘অ্যানিম্যাল হাউজ’, টেকনিশিয়ান, মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপ কিছুই ছিল না তাঁদের। সব কাজই নিজেদের করতে হয়েছে। সবকিছু নিজেদের হাতে করাতে সবকিছু নিজেদের মনের মতো করে তৈরি করে নিতে পেরেছেন। ভোর থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত কঠোর পরিশ্রমের ফল পেতে শুরু করেছেন বছর দুয়েক পর থেকে। ১৯৯৮ সালে তাঁরা প্রথম গবেষণা-শিক্ষার্থী পেলেন। ১৯৯৯ সালে পেলেন প্রথম আন্তর্জাতিক রিসার্চ গ্রান্ট – ইউরোপিয়ান কমিশন থেকে। নরওয়েজিয়ান একাডেমি অব সায়েন্স থেকে পান ‘ইয়ং সায়েন্টিস্ট অ্যাওয়ার্ড’। তারপর থেকে একদিনের জন্যও গবেষণা বন্ধ রাখেননি মে-ব্রিট ও এডভার্ড। তাঁরা গবেষণা কাজ এমন ভাবে ভাগ করে নিয়েছেন যেন একটুও সময় নষ্ট না হয়। মে-ব্রিট দেখেন ল্যাবোরেটরি ও প্রশাসন। এডভার্ড দেখেন কারিগরি দিক। কাজের ক্ষতি এড়াতে পারতপক্ষে কোন কনফারেন্সেই দু’জন এক সাথে যান না।
পথ ও পরিবেশের স্মৃতি সংরক্ষণে প্লেস সেলের ভূমিকার ব্যাপারটা গত শতাব্দীর শেষে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলেও প্লেস সেলগুলো শুধুমাত্র হিপোক্যাম্পাসেই থাকে নাকি হিপোক্যাম্পাসের বাইরেও থাকে সে ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায়নি তখনো। মোজাররা গবেষণা শুরু করলেন এ ব্যাপারে।
ইঁদুরের হিপোক্যাম্পাসে ইলেকট্রোড স্থাপন করে একটা বড় (দেড় মিটার দৈর্ঘ্য ও দেড় মিটার প্রস্থের) কাঠের বাক্সের ফ্লোরে ছেড়ে দেয়া হলো। বাক্সের ফ্লোর জুড়ে চকলেটের গুড়ো ছড়িয়ে দেয়া হলো যেন ইঁদুর খাবারের লোভে বাক্সের মধ্যে ছোটাছুটি করে। বাক্সের ফ্লোরের সাথে কম্পিউটারের সংযোগ ঘটানো হলো। ইঁদুরের হিপোক্যাম্পাসের প্লেইস সেলে কোন উত্তেজনা তৈরি হলে সেখানে স্থাপিত ইলেকট্রোডের সাহায্যে কম্পিউটার সেই ব্রেইন-সিগনাল রেকর্ড করতে পারে। ফ্লোরের কোন পথে গেলে ইঁদুরের প্লেইস সেলে উত্তেজনা তৈরি হয় তাও রেকর্ড হয়ে যায়।
মোজার দম্পতি আবিষ্কার করলেন যে হিপোক্যাম্পাসের বাইরে এন্টোরাইনাল কর্টেক্সেও প্লেইস সেলের সিগনাল পাওয়া যায়। তার মানে শুধু মাত্র হিপোক্যাম্পাসের প্লেইস সেলগুলিই যে পরিবেশের স্মৃতি তৈরি করছে তা নয়, এন্টোরাইনাল কর্টেক্সের সেলগুলোর ভূমিকাও আছে সেখানে। তাঁরা দেখলেন ইঁদুরের মগজের এন্টোরাইনাল কর্টেক্স থেকে যে সিগনাল আসছে তা ষড়ভুজের মত প্যাটার্ন তৈরি করছে। বোঝাই যাচ্ছে যে হিপোক্যাম্পাসের প্লেইস সেল ছাড়াও এন্টোরাইনাল কর্টেক্সের এক ধরনের সেলও কাজ করছে যা এই প্যাটার্ন তৈরি করছে। মোজাররা এই সেলের নাম দিলেন গ্রিড সেল।
গ্রিড সেল আবিষ্কারের ফলাফল প্রকাশিত হয় ন্যাচার জার্নালে ২০০৫ সালে [৫]। প্লেইস সেল ও গ্রিড সেলের সমন্বয়ে প্রাণির মস্তিষ্কে পরিবেশের স্মৃতি বা এপিসোডাল মেমোরি কীভাবে তৈরি হয় তার একটা পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া গেল [চিত্র ১৩]।
গ্রিড সেল আবিষ্কারের সাথে সাথে দ্রুত খ্যাতিমান হয়ে গেলেন মোজার দম্পতি। সারা পৃথিবীর নিউরো-সায়েন্টিস্টদের নজরে চলে এলো তাঁদের কাজ। ২০০৫ সাল থেকে শুরু করে ২০১৪ সালে নোবেল পুরষ্কার পাবার আগ পর্যন্ত আরো অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ পুরষ্কার পেয়েছেন এই বিজ্ঞানী দম্পতি। নরওয়ের ট্রোন্ডেইম বিমানবন্দরে বিখ্যাত নরওয়েজিয়ানদের চৌদ্দটি ফটোগ্রাফ টাঙানো আছে। তাদের মধ্যে তেরোটা ফটোগ্রাফই হলো বিখ্যাত খেলোয়াড় বা শিল্পীর। একটা মাত্র ছবি আছে মোজার দম্পতির – নরওয়ের বিখ্যাত বিজ্ঞানী দম্পতি।
মানুষের মগজে প্লেইস সেল ও গ্রিড সেল
ইঁদুর ও অন্যান্য প্রাণি যেভাবে পথ দেখে বা পরিবেশ মনে রাখে – মানুষের বেলায় তা কিন্তু আরো অনেক জটিল। মানুষ বহুমাত্রিক তথ্য ব্যবহার করতে পারে। ছবি, শব্দ, সময়, দূরত্ব ইত্যাদি অনেকগুলো অপেক্ষক মানুষ ব্যবহার করতে পারে। তাই মানুষের বেলায় প্লেইস সেল ও গ্রিড সেলগুলোর ভূমিকা আরো অনেক বেশি জটিল। কিন্তু তারপরেও অনেকগুলো পরীক্ষায় মানুষের হিপোক্যাম্পাসের প্লেইস সেলের পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে। লন্ডনের ট্যাক্সি-ড্রাইভারদের মগজের এম-আর-আই স্ক্যান করে দেখা গেছে – যেসব ড্রাইভার দীর্ঘ প্রশিক্ষণ ও অনুশীলনের পর ট্যাক্সি ড্রাইভিং লাইসেন্স পেয়েছেন – তাদের হিপোক্যাম্পাসের আয়তন ও গঠন সাধারণ মানুষের হিপোক্যাম্পাসের আয়তনের তুলনায় বেশ কিছুটা বদলে গেছে। দুটো গবেষণাপত্রে এই ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে [৬,৭]। ড্রাইভিং ট্রেনিং শুরুর আগের হিপোক্যাম্পাস আর ট্রেনিং শেষের হিপোক্যাম্পাসে অনেক পার্থক্য দেখা গেছে। সেলুলার লেভেলে জৈব বিবর্তনের সরাসরি প্রমাণ হিপোক্যাম্পাসের এই পরিবর্তন।
চিকিৎসাবিজ্ঞানে ও’কিফ এবং মোজারদের আবিষ্কার ব্যাপক সম্ভাবনার দরজা খুলে দিয়েছে। আলজেইমার্স, ডিমেনসিয়া সহ আরো অনেক মানসিক রোগের কারণ নির্ণয় ও তাদের চিকিৎসা সংক্রান্ত গবেষণায় দ্রুত উন্নতি হবে সে ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই।
তথ্যসূত্র
[১] E. C. Tolman, Cognitive maps in rats and men. Psychological Review, 55, 189-208 (1948).
[২] J. O’Keefe, and J. Dostrovsky, The hippocampus as a spatial map, Preliminary evidence from unit activity in the freely-moving rat. Brain research 31, 573-590 (1971).
[৩] J. O’Keefe, and L. Nadel, The Hippocampus as a cognitive map, Oxford University Press (1978).
[৪] May-Britt Moser and Edvard I Moser, Crystals of the Brain, EMBO Mol Med 3, 69-71 (2011).
[৫] T. Hafting, M. Fyhn, S. Molden, M-B, Moser, E. I. Moser, Nature 436, 801-806 (2005).
[৬] K. Woollett, and E. A. Maguire, Acquiring “the Knowledge” of London’s layout drives structural brain changes. Current Biology,, 21 (24), 2109-2114 (2011).
[৭] E. A. Maguire, D. G. Gadian, I. S. Johnsrude, C. D. Good, J. Ashburner, R. S. Frackowiak, and C. D. Frith, Navigation related structural change in the hippocampi of taxi drivers. PNAS, 97 (8), 4398-4403 (2000).
[৮] www.nobelprize.org