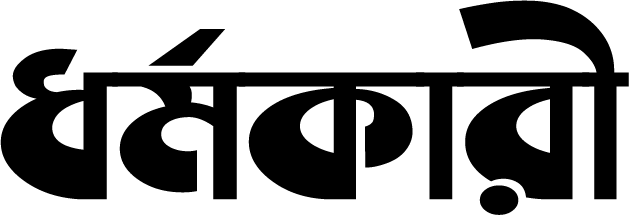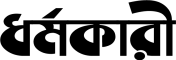লিখেছেন মোজাফফর হোসেন
১.
সৈয়দ রহমান পপুলার ডায়গোনস্টিক সেন্টারের তিনতলার কেবিনে শুয়ে। পাশে স্ত্রী শায়লা আধবসা। শায়লার শরীরটাও বিশেষ ভালো যাচ্ছে না। তার ওপর কয়েকরাত না-ঘুম কাটানোয় প্রথম দর্শনে কে মূল রোগী ঠাওর করা যায় না। কেবিনের এক কোণায় চেয়ারপেতে বসা স্বপ্ন- ছেলেবৌ। খানিক আগে এসেছে। দুই ছেলেবৌ আর এক মেয়ে এখন পালা করে আসছে। শুরুর দিকে সকলে একসঙ্গে এসে ভিড় জমাতো বলে হাসপাতাল কর্র্তৃপক্ষ ভীষণ বিরক্ত হত, এখন ওরা নিজেরাই বিরক্ত হয়ে আসে না। আসতে হয় তাই পালা করে আসা। স্বপ্না ঘড়ির দিকে তাকালো, মাত্র আধাঘণ্টা হল। হাসপাতালে সময় যেন যেতেই চায় না। এখানে জীবনটা বড্ড স্থির আর একঘেয়ে।
সকালে দেরি করে বিছানা থেকে উঠাটা স্বপ্নার অভ্যাস। চাইলেই সন্ধ্যা শিফটের দায়িত্ব নেয়া যেত, কিন্তু তাতে করে জি-বাংলার সিরিয়ালগুলো মিস হতো। তারচেয়ে বরং ঘুমটা কামায় দেয়া ভালো। তাছাড়া ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে আজকাল শরীরটাও মুটিয়ে যাচ্ছে। বিয়ে-বাচ্চা-সংসার সবমিলে ফিগারটা এমনিতেই গেছে, যেটুকু আছে একটু মেইনটেইন না করলে তাও টিকবে না। স্বপ্না ভাবে, ভাবতে ভাবতেই জিজ্ঞেস করে, ‘মা দেখেন তো, লেগিংস আর ফতুয়াতে আমাকে কেমন মানাচ্ছে?’
‘মানাচ্ছে মা!’ শায়লা দেখে কি না-দেখে উত্তর করেন। শাশুড়ির নিরাসক্ত উত্তর শুনে আরো কি কি জিজ্ঞেস করতে গিয়ে দমে যায় স্বপ্না। কেবিনের থাই গ্লাসে নিজের অবয়বটা আরো একবার পরখ করে- দাঁড়িয়ে শরীরটা এদিক-সেদিক করে দেখে। ‘আর একটু ঝরাতে হবে’ – নিজেকেই নিজে বলে।
রহমান আধো ঘুম, আধো জাগা। আজ তিনদিন থেকেই এই অবস্থায় আছেন। স্বপ্নে বায়স্কোপ দেখছিলেন। পাকুড় গাছের নিচে বসে লাল-নীল রঙের ফিতায় সজ্জিত বাক্সের ছিদ্রপথে দৃষ্টিচুবিয়ে উপভোগ করছিলেন নিজেরই বাল্যকালের কোলাজচিত্র। একের পর এক চিত্র এক একটা স্মৃতি নিয়ে আসে যেন! সেদিন ঘুম ভেঙে গেলেও পুরোপুরি স্বপ্নের জগত থেকে ফেরাতে পারেননি নিজেকে। একচোখ তার আটকে আছে বায়স্কোপে, অন্যচোখে অনীহা নিয়ে দেখছেন কেবিনের দেয়ালের মরা একটি দুটি মাছি আর থেকে থেকে কয়েকটি পাকা টিকটিকির উৎপাত। একেকবার একেক চোখ বন্ধ করে দুই জীবনের মধ্যে তিনি আসা-যাওয়া করছেন, কখনো কখনো দুটি চোখ খোলা রেখে একসঙ্গে যাপন করছেন দুইজীবন। থেকে থেকে কি সব আপাত অর্থহীন কথাবার্তা বলছেন। সেগুলি যেমন বিরক্তিকর তেমন উপভোগ্যও। নাতনি এলিটা আর লিজা থাকলে তো হেসে কুটি কুটি হয়। এটাসেটা বলে উসকে দেয়ার চেষ্টা করে।
হঠাৎ করেই নিজের অণ্ডকোষটা হাত দিয়ে চেপে ধরলেন রহমান। ‘শ্যালা মফায়, এভাবে কেউ মারে?’ আলটা আলটা গলায় বললেন তিনি।
ফের শুরু হল। শায়লা নড়েচড়ে বসলেন।
‘মফা কে মা?’ স্বপ্না জিজ্ঞেস করে।
‘বোধহয় ওর চাচাতো ভাই মফেদুলের কথা বলছে।’
‘ওহ!’ স্বপ্না আর আগ্রহ দেখায় না।
‘আমি তো আর আড়ি করি মারিনি। বলটা তুই ওইভাবে ঠেকাতি গেলি ক্যানে? কিছুক্ষণ শুয়ি থাক, ঠিক হয়ি যাবে।’ মফেদুল বলে।
রহমান হাত পা ছেড়ে দেন। অসুবিধা হচ্ছে দেখে শায়লা পায়ের তলের বালিশটা বের করে দেয়। ওপরের দিকে মাথাটা তুলে একটা টানা নিঃশ^াস নেন। ‘আহ! কি নীল।’ ঘাসের ওপর শুয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে বলে রহমান।
‘রহমান ওঠ। ওঠ বুলছি, অ্যাটাকে আসছি।’ সবুর নিচ ব্যাক। ব্যতিব্যস্ত হয়ে রহমানকে ডাকে। রহমান কোনো সাড়া দেয় না। আকাশের দিকে তাকিয়ে ভেসে যাওয়া আলগা মেঘগুলোকে থামিয়ে কি যেন আঁকার চেষ্টা করে।
‘রহমান ওঠ, ওঠ। গোলটা হয়ে গেল তো!’ বিছানায় শুয়ে শুয়ে নিজের নাম ধরে ডাকেন রহমান।
‘ইশরে! হল তো।’ রহমান আবার বলেন।
‘কি হলো বাবা?’ স্বপ্না জিজ্ঞেস করে।
‘গোল! গোলটা হয়ি গেল। জিততি জিততি হেরি গ্যালাম মধু। আব্বার পকোটে একমাসে হাত চালি একশ ট্যাকা হয়লো। সবটা গেল।’ পুকুরে পা ধুতে ধুতে কথাগুলো বলে রহমান। ওপরে গামছা হাতে দাঁড়িয়ে মধুমালা। রহমান মধুমালাকে বাড়িতে পাঠিয়েছিল গামছা আনতে। মাত্রই এলো।
‘এত হারিস যেকুন, তেকুন টাকা দি না খেললিই পারিস। বুললাম, জুমাতের ভ্যান থেকি আমাকে একটা মালা কিনি দে। দিলি নি তো, এখুন বোঝ!’ মধুমালা টিটকিরি মেরে কথাগুলো বলে।
‘দিতাম তো। ট্যাকাটা দ্বিগুণা করি তোকে মালার সাথে টালাও দিতাম।’
‘টালা আবার কি?’
‘একুন আর বুলি লাভ কি?’
‘না, বল না দেখ।’ আবদার করে বসে মধুমালা।
রহমান হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে থেকে চোখ বন্ধ করে মধুমালা আর রহমানের আলাপ শোনেন। মাঝে মধ্যে মনে হলে তিনি নিজেও সেই আলাপে অংশ নেন।
‘আর একদিন জিতি তেকুন বুলবু।’ জবাব দেয় রহমান।
‘তালি আর গামছা দিলাম না। যেদিন জিতবি সেদিন দেবো।’ বলে মধুমালা পা বাড়ায় বাড়ির দিকে।
‘এই মধু শোন। শুনি যা। যাসনি বুলছি। ভেজা গা তো! এভাবে বাড়ি গেলি মা বকি রাকবি না!’ স্বর চড়া করে বলে রহমান।
‘বকুক। সেটাই তো আমি চাই।’ বলে মধুমালা চোখের আড়াল হয়ে যায়। রহমান কিছুক্ষণ একা বসে থাকে। সন্ধ্যার আধোছায়া আধো আলোতে পুকুরের কালচে নীল জলে মাছের পোনাগুলো সব ওপরে ভেসে ওঠে। সন্ধ্যের শেষ আলোয় ওরা স্নান সেরে নেয়। রহমান মায়াভরে দেখে। ‘কি আনন্দময় জীবন!’ বিছানা থেকে ঘাড়টা ঘুরিয়ে বলেন রহমান।
‘সারারাত আমাকে ঘুমুতে দেয়নি। বুকটা জ্ব্লে গেল, জ্বলে গেল বলে বাচ্চার মতো কেঁদেছে। আর এখন বলছে- কি আনন্দময় জীবন!’ শায়লা ক্ষোভে-রাগে কথাগুলো আপন মনে বলেন।
‘মা কাল রাশির বাড়ি যাওয়া হয়নি।’ গুণ গুণ করা থামিয়ে বলে স্বপ্না।
‘বলিস কি?’ সহসা খানিকটা চাঙ্গা হয়ে ওঠেন শায়লা বেগম; কিংবা চাঙ্গা হয়ে ওঠার ভান করেন তিনি।
এরপর ইরার মুখ থেকে গতপর্বের সারকথা শোনেন।
২
‘দ্যাক, এভাবে সবসুময় আমি শাগ তুলবু আর তুই ঘুঘুর পেছনে দৌড়ুবি; আর বাড়ি ফিরার সুময় আমার তুলা আদ্দেক নি চাচিকে বুলবি, তুই তুলিছিস, এটা হবে না। আজ তুই আমার সাথে শাগ তোল, না হলি আমি আর ভাগ দেবো না।’ ফিনফিনে গমের জমিতে সাদা-মসৃণ পাদুটো চুবিয়ে কথাগুলো বলে মধুমালা।
‘ওসব বতু তুলা আমাক দি হবে না।’ উত্তর করে রহমান।
‘তালি কি হবে শুনি? পাখি ধরা? একটাও ধরিছিস এতকালে?’
‘আমি পাখি ধরতি যাই, একথা তোকে কে বুললু? আমি যাই পাখিদের সাথে মিলামিশা করতি। তাদের ভাষা বুঝতি।’
‘যে আমার ভাষা বোঝে না, সে বুঝবি পাখিদের ভাষা!’ মুখের কোনো ব্যঙ্গ হাসি হেসে বলে মধুমালা।
‘ক্যাচক্যাচি পাখি চিনিস?’ প্রশ্ন করে রহমান।
‘ওড়ার ক্ষমতা নেই! খালি ক্যাচক্যাচ করে।’
‘তোর কাছে মনে হয় খ্যালি ক্যাচক্যাচ। উরা আসলে মেলা কথা বলে।’
‘কি বলে তার একটা নমুনা দেতো শুনি।’
‘সেদিন আমি মবুর আমবাগানে গিছি ঘুঘুর তল্লাসে। দেকি, আমাকে দেকি একটা ক্যাচক্যাচি পাখি আরেকটাকে বুলচি, ক্যাচ ক্যাচ! ক্যাচ ক্যাচ!’
‘ক্যাচ ক্যাচ! ক্যাচ ক্যাচ!’ ভেংচি কেটে কথা ভাঙায় মধুমালা।
‘ঠিক হচ্ছে না মধু!’ শাসিয়ে বলে রহমান।
‘ক্যাচ ক্যাচ তো আমিও বুঝলাম। মানে কি ক?’
‘ও আসলে বুলছিল, ঐ দেখ যে ছেলিটা আসছি ওর পাছে পাছে একটা পাগলি থাকে, তার গা-দি’ গবরের গন্ধ বেরুই! ওয়াক! ছিঃ!’
‘তালি, সেদিন আমাদের একসাথে দেকি একটা গরু কি বুলছিল বুলি?’ তড়িৎ ভেবে নিয়ে মুখে দুষ্টু হাসি হেসে বলে মধুমালা।
‘বুলা লাগবি না। গরুর ভাষা যে তুই বুঝিস তা আমি জানি। যে যার জাত, সে তার ভাষা বোঝে। এটা আমি না, জ্ঞ্যানি মানষে কয়।’
‘তাইলে তো তুই ক্যাচক্যাচি পাখি। ক্যাচ ক্যাচ! ক্যাচ ক্যাচ!’
‘হলাম। আমার তো এতে আপত্তি আছে বুলিনি। পাখি হওয়া কত ভাগ্যির বুঝিস তুই? যেমনে খুশি উড়ি যাওয়া যায়। একদিন দেখিস, আমি ঠিকই উড়ি যাবো।’
‘আমাকে সাথ নিবি?’
‘পাখি গরুকে সাথ নেয় কেমুন করি! মেলে তুই ক?’
‘যাহ, তুই তোর পাখির কাছে। তোর সাথে বকবক করলি আজ আর বতু তুলা হবে না।’
রহমান লাফাতে লাফাতে পাশের সেগুন বাগানের ভেতর দিনে দুপুরে অদৃশ্য হয়ে যায়। কিছুক্ষণ সেই শুণ্যতার দিকে তাকিয়ে থাকে মধুমালা। তারপর খানিক দূরে শাখ তোলা ছেলেমেয়েদের দিকে এগিয়ে যায়।
৩.
‘কুক… কুক…কুউক…!’ রহমান ডাক দিয়ে ঘুঘু ডাকে।
‘কুক… কুক…কুউক…!’ একটা ঘুঘু শিশুগাছের মগডাল থেকে উত্তর নেই।
‘কুক… কুক…কুউক…!’ রহমান বিছানা থেকে পাল্টা জবাব দেয়ার চেষ্টা করে। শব্দগুলো কেমন এলোমেলো হয়ে বিশ্রি শোনায়।
‘মা, বাবা মনে হয় মেন্টালি আর সাউন্ড নেই। খালি আজে বাজে বকছে কয়দিন থেকে।’ ইরা বলে।
ইরা মেজো বৌ। ছোটবৌ স্বপ্না উঠে যাওয়ার ঘণ্টাদুয়েক পর ইরা এলো। স্বপ্না থাকতে থাকইে দুপুরের খাওয়া-গোসল সেরে নিয়েছেন শায়লা বেগম। ঘণ্টাখানেক ঘুমিয়ে ঘুমের নেশাটা আরো বেড়ে গেছে। কিন্তু রহমানের আচরণগত পরিবর্তনে ঘুমানো সম্ভব হচ্ছে না। মানসিক একটা সমস্যা নিশ্চয় হয়েছে। কিন্তু তার চেয়ে বড় কথা, কিডনি ফেইলর ও হার্ট অ্যাটাক। যদিও মাইনর অ্যাটাক, তবে বিশেষ কেয়ারে না রাখলে বড় কিছু হয়ে যেতে পারে। ডাক্তার বলেছেন, আপাতত কিডনি আর হ্যার্টের ট্রিটমেন্ট চলুক, পরে মানসিক ব্যাপার নিয়ে ভাবা যাবে। শরীরটা সুস্থ্য হলে অটোমেটিক সেরেও উঠতে পারেন।
‘ডাক্তার তো বলছেন ঠিক হয়ে যাবে।’ শায়লা ইরার সঙ্গে সঙ্গে নিজেকেও আস্বস্ত করেন।
‘মা, মাথার সমস্যা হলে ভেবে দেখেন, কি সমস্যায় না পড়বো আমরা! ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে উঠছে, বাড়িতে কতো বাইরের লোকজন আসে। একটা প্রেস্টিজ ইস্যু হয়ে দাঁড়াবে না?’
‘বউমা তোমার শশুর এখানো পাগল হয়ে যাননি। আর তাছাড়া তোমার বাসাতেও সে পাগলামো করছে না।’ শক্তগলায় কথাগুলো বলতে গেলেন শায়লা। কিন্তু পারলেন না। হাসপাতালের অর্ধেক খরচই চালাচ্ছে ইরার স্বামী, অর্থাৎ শায়লা-রহমানের মেজো সন্তান। কথাটা ভেবে কণ্ঠস্বর নত করে বললেন, ‘দোয়া করো বৌমা, তা যেন না হয়।’
‘রাইট মা।’ ইরা বলে। ‘দোয়া তো কম করছি না। সান্টুর কাল থেকে এক্সাম। ওর পাশে না বসে থাকলে পড়তেই বসে না। ছেলেটা যা নটি হয়েছে না মা! গতবার একটা নম্বর কম পাওয়ায় রোল দশে নেমে গেছে। এবার যে কি হবে, আল্লাহ নোজ! সারাদিন হাসপাতাল আর জায়নামাজে বসে দোয়া করতে করতেই কেটে যাচ্ছে। বাবা ভালো হলে, আমি আর আপনার ছেলে ঠিক করেছি আজমির শরিফে সিন্নি দিয়ে আসবো। ভালো হবে না মা?’
‘গতবছরই না তোমার মায়ের জন্য মানত করেছিলে। তোমরা বোনসকলে ঘুরে এলে আজমির শরীফে।’
‘গিয়েছিলাম। কিন্তু ঘোরা আর হল কই? আমরা কেবল আজমির শরীর আর শহরের লেকগুলো ঘুরে দেখতে পেরেছি। তখনই তো বাবা বিছানায় পড়ে গেলেন। আপনার ছেলে বলল, তিনদিনের মধ্যে চলে আসতে। কত কি দেখতে বাকি থেকে গেল, এবার গেলে পুরো রাজস্থান ঘুরে আসবো।’
ইরার কথায় আগ্রহ পায় না শায়লা। তবুও কি এক অজানা কারণে তাল দিতে হয় তাকে।
‘যেও মা। তোমাদের তো এখনই বেড়ানোর বয়স। আমার মতো বয়েস হলে আর কিচ্ছু দেখা হবে না। তোমার শশুরের সঙ্গে নামেই কানাডায় থাকলাম। নায়াগ্রা ফলস্ পর্যন্ত দেখা হল না। তোমার শশুর এনজিওর কাজটা নিয়ে কম শহরে তো আর ঘুরলো না। সবখানেই তার একই স্বভাব। অফিস শেষ করে সোজা বাড়ি এসে ঘরের মধ্যে লাইট অফ করে বসে থাকা। এভাবে থাকলে কি আর ঢাকা-টরেন্টো আলাদা করা যায়, বলো?’ শায়লা কথাগুলো শেষ করে দেখেন ইরা কানে হেডফোন লাগিয়ে কার সাথে যেন ফিসফিস করে কথা বলছে। নীরব হয়ে যান তিনি।
৪
‘মধু, এক দৌড়দি একমগ পানি নি আয় তো। খাবো।’ রহমান হাপাতে হাপাতে বলে। বউতোলা খেলায় রহমানের দক্ষতা হিংসে করার মতো। মধুমালা ওদের বাড়ি থেকে বদনা ভরে পানি নিয়ে আসে।
‘পানি! পানি!’ খুব কষ্ট করে বলে রহমান। ইরা পানির বোতলটা তুলে ধরে। শায়লা গ্লাসের অর্ধেক ভরে রহমানের মাথা তুলে ধরে খাওয়ানোর চেষ্টা করেন।
‘বদনায় পানি?’ ক্ষেপে যায় রহমান।
‘বাবা, বদনা হবে কেনো? গ্লাস। এখানে বদনা আসবে কোত্থেকে!’ ইরা বোঝানোর চেষ্ঠা করে। মুখের কোনে তার চিকন হাসি।
‘আরে, ওজুর বদনা। আব্বা এই বদনায় ওজু করে, পানিও খায়।’ মধুমালা রহমানকে বোঝায়। রহমান বদলার নলটা মুখের মধ্যে নিয়ে ঢকঢক শব্দে পানি গিলতে থাকে।
‘রহমান হাগার বদনায় পানি খায়। ওই বদনায় নইতন বুড়ি ছোঁচে’ – বলে চেঁচিয়ে পাড়াময় করে তোলে বাচ্চু। রহমান বদনা ফেলে বাচ্চুর দিকে তেড়ে যায়।
একঝটকায় শায়লার হাতে ধরা গ্লাসটি ফেলে দেন রহমান। ‘তোর একদিন কি আমার একদিন। শ্যালা বাচ্চু! চিবিয়ে চিবিয়ে কথাগুলো বলেন।’ সবটা বোঝে না শায়লা-ইরা।
‘আম্মা, বাবা কি-সব নাম বলেন, কাউকে চেনেন আপনি? তাদের কাউকে এখানে ডাকলে হত না? বাবা খুব খুশি হতেন।’
‘কারো কারো নাম শুনেছি ওর মুখে। সবাই হয়ত আর বেঁচেও নেই।’
‘বাবার বন্ধু না আত্মীয়?’ ইরা প্রশ্ন করে।
‘আমি তো কখনই ওর গ্রামের বাড়ি যাইনি। আমার শশুর দ্বিতীয় বিয়ে করার কারণে শাশুড়ি ওকে নিয়ে ঢাকায় ভাইয়ের বাসায় চলে আসেন। আমার শাশুড়িপক্ষের অবস্থা বেশ ভালো ছিল, সকলে শিক্ষিত। তারপর শাশুড়ি আর ওকে গ্রামে যেতে দেননি, যদি না ফেরে- এই ভয়ে। আমরা কানাডায় থাকাকালীন শশুর মারা যান। কয়েকবছর পর শাশুড়িও গত হলেন। এরপর তোমার শশুরের মুখে আর কখনো গ্রামের বাড়ির বা আত্মীয়স্বজনের গল্প শুনিনি। দেশে ফিরে এলাকার মানুষজনকে না চেনার ভান করে এড়িয়ে যেতে থাকলো। গ্রামের কথা তুললেই ক্ষেপে যেত। বলতো, গ্রামে মানুষ বাস করে নাকি! এ নেই, সে নেই। যত সব মুর্খের বাস! আমি মেহেরপুরের এক আমব্যবসায়ীর মুখে শুনেছি, ওর দ্বিতীয় পক্ষের এক ভাই ছিল। সেই গ্রামের বাড়ি-জমিজমা দেখাশুনা করত।’
‘মা, আমি মামাবাড়ি যাবো না। শহর আমার ভাল্লাগে না।’ শায়লার মুখের দিকে মুখটা তুলে পিটপিট করে তাকিয়ে কথাগুলো বলেন রহমান।
‘আচ্ছা যেতে হবে না।’ মাথায় হাতটা রেখে উত্তর করেন শায়লা। তৃপ্তিতে চোখটা বন্ধ করেন রহমান।
‘চল, তোর ভালো না লাগলি চলি আসবি। আমি তো আর তোকে জোর করে আটকাচ্ছি না।’ মা কুরুচে উলের সুতা দিয়ে স্যান্ডো গেঞ্জি বুনতে বুনতে বলেন।
‘কেন্তু তুমি তো একেবারেই যাচ্ছো? তুমার ওকিনে যদি ভালো না লাগে? ফিরি আসবা?’ রহমান প্রশ্ন করে।
‘না।’ দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর করেন মা।
‘তালি আমি?’
‘হয় একিনে থাকবি, না হলি মা’র সঙ্গে থাকবি। তোর সিদ্ধান্ত।’
‘শক্ত সিদ্ধান্ত মা।’
‘শক্ত কেনে? মা’র চেয়ি ওমুন বাবাই তোর কাছে বড় হয়ি গেল? সৎমা’র সংসারে থাকতি পারবি?’ মা প্রশ্ন করেন।
‘ব্যাপারটা শুধু বাবা আর সংসার না। একিনে আরো অনেক কিছু আছে আামার।’ বোঝানোর চেষ্টা করে রহমান।
‘কি আছে শুনি?’ মা কুরুচ বোনায় মনটা চুবিয়ে জানতে চান।
‘কি করে বোঝায় মা?’ রহমান নিজেও বুঝে উঠতে পারে না ঠিক কি কি আছে এখানে।
বিছানায় শুয়ে শুয়ে ‘ক্যাচ ক্যাচ! ক্যাচ ক্যাচ!’ শব্দ করে চলেন রহমান। ‘কুক… কুক…কুউক…!’ ডেকে ওঠার ব্যর্থ চেষ্ঠা করেন।
‘তুই বড় হয়ি গিছিস।’ মা বলেন। ‘এজন্যিই তোকে জোর করছি নি। তোর ভালো আমি তোর ওপরে ছেড়ি দিলাম। তবে এটুকু বুলি রাখি, তোকে ছাড়া তোর মা বাঁচবি না।’
৫.
‘মা তুমি সারাদিন বাবার এমন অদ্ভুত আচরণ টলার করো কি করে? এত শিক্ষিত মানুষ এমন ননসেন্স বিহ্যাভ করে কি করে?’ শোয়েবকে বেশ উত্তেজিত দেখায়। শোয়েব রহমানের ছোটো ছেলে।
‘এভাবে বলিস না ছোটো।’ বড়বোন সাদেকা শোয়েবকে থামিয়ে দেয়।
‘বলবো না? সেদিন কি হয়েছে জানো আপা, বাবা ইরাকে কি বিশ্রি একটা কথা বলেছে। বলেছে, তোমার…! ছিঃ আমি ভাবতেও পারছি। ছেলেবৌকে কেউ একথা বলে?’
‘ওটা ইরাকে না, মধুকে বলেছে।’ শায়লা উত্তর দেন।
‘এই মধুটধু আবার এলো কোত্থেকে? বাবার কি অন্যকোথাও প্রেমটেম ছিল, মা? কি একটা সিনেমাটিক নাম! ডাজ শি রিয়েলি এক্সিস্ট?’ বিরক্তির সুরে প্রশ্ন করে শোয়েব।
‘বাইরে সফিক তোর জন্যে অপেক্ষা করছে। একটা জরুরী আলাপ আছে।’ সাদেকা শোয়েবকে ঘর থেকে ঠেলে বের করে দেয়। সফিক তাদের মেজোভাই। পেশায় আইনজীবী। ঢাকায় ভালো নামডাক আছে তার। সফিক আর শোয়েব হাসপাতালের ক্যাফেটেরিয়ায় বসে।
‘বাবাকে দেখে কি মনে হল?’ সফিক কথা পাড়ে।
‘ম্যাড! টোটালি ম্যাড!’ শোয়েব উত্তর দেয়।
‘আমি সেটা বলছি না। মানে আর কতদিন বলে মনে হল? আমার তো মনে হয়, বাবার সময় শেষ। ডাক্তারও আমাকে আকারে ইঙ্গিতে সেটাই বললেন। নো ইম্প্রুভমেন্ট। যে কোনো সময় একটা কিছু হয়ে যেতে পারে।’
‘কি বললে? না না অসম্ভব। বাবা চলে গেলে আমি ঝগড়া করবো কার সঙ্গে?’ বলেই হাউমাউ করে কেঁদে ফেলার উপক্রম হয় শোয়েব।
‘কুল ডাউন। আমরা তো চাই বাবা বেঁচে থাকুক, নাকি? কিন্তু সিদ্ধান্ত তো ওপরআলার হাতে। এখন প্রশ্ন হল, বাবার হঠাৎ করে কিছু একটা হয়ে গেলে, কোথায় কবর দেয়া হবে- এসব কি আমরা ঠিক করেছি?’
‘জানি না।’ শোয়েব ছোট্ট করে উত্তর দেয়। জানার ব্যাপারে তার আগ্রহ আছে বলেও মনে হয় না।
‘কিন্তু জানতে তো হবেই। লাশ হয়ে গেলে তো আর বাবাকে আমরা হাসপাতাল-বাড়ি কোথাও রাখতে পারবো না।’
‘তুমি কি ভাবছ?’
‘বড় আপার সঙ্গে কথা বললাম। আমরা সকলে থাকি গুলশানে। আশেপাশে কবর দেয়া হলে ভালো হত।’
‘হুম। তাহলে তাই করো। আমার কোনো আপত্তি নেই।’
‘কিন্তু এদিকে কবরস্থানের দাম কত জানিস? বাবা তো কিছু রেখে যাননি। আমরা তার চিকিৎসার জন্যে তো আর কম করছি না। সামনে বছর আমার ইত্র পড়াশুনার জন্যে কানাডা যাবে। আমি সেই খরচ গোছাতেই হিমশিম খাচ্ছি। বড়ভাই জাপান থেকে কোনো রেসপন্স করছে না। আমি আর তুই কত পারবো বল?’
‘তাহলে কোথায় ব্যবস্থা করতে চাইছো। আজিমপুর, জুরাইন?’ শোয়েব জিজ্ঞেস করে।
‘মা বলেছেন, কম করেও ২৫ বছর মেয়াদে যেন বাবার কবরটা দিই আমরা। এটাই নাকি আমাদের কাছে তার শেষ চাওয়া। আমি খোঁজ নিয়ে জেনেছি, এই মেয়াদে মিরপুর বুদ্ধিজীবী কবরস্থান, উত্তরা সেক্টর ১২নং কবরস্থান, আজিমপুর কবরস্থান ও জুরাইন কবরস্থানে খরচ হবে ১১ লক্ষ টাকা।’
‘আর বনানী ও উত্তরা ৪নং সেক্টর কবরস্থানে?’
‘ওখানে আরো বেশি। ১৫ লক্ষ টাকা। আবদুল্লাপুরের ঐদিকে একটা কবরস্থান আছে। বেশ সস্তা আবার নতুনও। ওয়েল অ্যারেঞ্জড্। তুই কি বলিস?’
‘কিন্তু একটু বেশি দূর হয়ে গেল না?’
‘তা হল। আমরা বিশেষ দিনগুলোতে গেলাম। তোর-আমার-বড়আপার গাড়ি আছে। শহরের বাইরে আমাদের খুব একটা যাওয়া হয় না। এই সুযোগে না হয় গেলাম।’
‘আম্মার একটা মত নেয়ার দরকার আছে না?’
‘মা কি বলবেন? মা’র কথা রাখতেই তো আমাদের এই সীদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে। কোনো মেয়াদি না হলে তো আমরা যে কোনো কবরস্থান বুক রাখতে পারতাম। মা তো আমাদের কাছেই থাকছেন, নাকি? বড়বোন মায়ের খোঁজ নেবে ভেবেছিস। দুদিন পরপর এসে মাতব্বরি ফলাবে। বড়ভাই ভাবিদের নিয়ে জাপানেই থেকে যাওয়ার বন্দোবস্ত করছে। আমরা হলাম কি যে গিনিপীগ। সব বুলডোজার আমাদের ওপর দিয়েই যায়।’
‘কাউকে না কাউকে তো করতে হয়।’
‘সে জন্যেই তো আমরা করে চলেছি। শোন, তোর শায় থাকলে একটা কাজ করতে পারি। বাবার বাবার কিছু সম্পত্তি আছে গ্রামে। বাবার সৎভাইয়ের ছেলেরা সেটা ভোগ করছে বলে খোঁজ নিয়ে জেনেছি। আমরা একটা শক্ত করে কেইস ঠুকতে পারলেই, একটা মোটা অংশ পেয়ে যাই। তুই কি বলিস? আমি সব করবো, তুই খালি সঙ্গে থাকবি।’
‘ভাইয়া, আমাকে একটু উঠতে হবে।’ বলেই উঠে পড়ে শোয়েব।
‘ওকে। জানিয়ে রাখলাম, ভেবে দেখিস।’ শেষ কথাটা বলে সফিক।
৬
কেশে ওঠেন রহমান। মিনিট পাঁচেক টানা কাশেন। জ্বরটা এখনো নামেনি। খানিক আগে সাবোসিটার দিয়েছেন শায়লা। আশা করছেন কিছুক্ষণের মধ্যেই কমে যাবে। জ্বর থাকা অবস্থায় রহমানের উল্টোপাল্টা কথা বলার মাত্রাটা আরো বেড়ে যায়।
-‘মা আমি একটু মবুর বাগান থেকি ঘুরি আসি?’ রহমান অনুরোধের সুরে বলে।
‘সময় নেই। চুয়াডাঙা থেকি দুটোর ট্রেন ধরতি হবে। একিন থেকি কম করিও ঘন্টা দুয়েক সময় হাতে নি বেরুতি হবে।’
‘আমি এই আলাম বুলি’ – বলেই অনুমতির অপেক্ষা না করে দৌড় দেয় রহমান। মা আজি যাচ্ছে এটা ঘণ্টাখানেক আগেও টের পেতে দেননি। বাবা রহমানকে আটকে দিতে পারেন, এই ভয়ে চেপে গেছেন। এখন সুযোগ মতো মেহেরপুর থেকে বের হতে পারলেই যেন মায়ের সকল চিন্তার অবসান ঘটে। রহমান এই যায়, এই আসে। হয়ত মাঝপথ থেকেই ফিরে এসেছে। কোনো কিছুই যেন সে বুঝে উঠতে পারে না। ঘুমের ঘোরে চলার মতো করে সে মাকে অনুসরণ করে। কার কথা যেন ভাবতে থাকে। এতটা পথ সে ভাবতেই থাকে। ট্রেনে উঠে বসার পর তার নামটা মনে আসে।
‘মধু!’ রহমান জ্বরগায়ে শরীরের সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করে উচ্চারণ করেন।
‘যাসনে রহমান! যাসনে! নেমে পড়! ওটা মরণফাঁদ! রহমান!’ ট্রেন ছাড়ার আগমুহূর্তে সতর্ক-হুইসেল দেয় স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকা তেলচিটচিটে খাঁকি পোশাক পরা আধাবয়স্ক লোকটি। পেছনে চিৎকার করে দৌড়ে আসে মালা। রহমান ট্রেনের জানালা গলিয়ে পেছন ফিরে তাকায়। কেমন কুয়াশাছন্ন হয়ে আসে চারপাশ। রহমান খুব শক্তি দিয়ে চোখের পাতা মেলে ধরার চেষ্টা করেন। শায়লা রহমানের দিকে এগিয়ে যান। আজ দুদিন পর রহমান একটু রেসপন্স করেছেন। মরার মতো পড়ে ছিলেন। রহমানের একটু নড়ে ওঠায় শক্তি ফিরে পান শায়লা। এই সংসারে এই শরীরটাই এখন তার একমাত্র শক্তি, এটুকু এ কয়দিনে ভালো মতোই বুঝেছেন তিনি। শায়লা যেন জোর করে রহমানকে বাঁচিয়ে রাখতে চান, নিজের প্রয়োজনেই।
ট্রেন হাটার গতিতে চলা শুরু করে।
‘যাসনে রহমান! যাসনে! নেমে পড়! ওটা মরণফাঁদ! রহমান!’ মধুমালা আরো একবার চিৎকার দিয়ে বলে ওঠে। মধুমালার চেহারা রহমানের চোখের সামনে ভেসে ওঠে। ট্রেনে রহমানের একটা হাত ধরে বসে আছেন মা, অন্য হাত ধরে যেন টানছে মধুমালা। যে কোনো একজনকে এখন বেছে নিতে হবে তাকে। রহমান ট্রেনে থাকলে হাসপাতালের রহমান সত্যি হয়ে ওঠে। আর রহমান নেমে গেলে স্বপ্নে বায়োস্কোপের সেই বালক সত্য হয়ে ওঠে।
‘আসিস না রহমান। আসিস না। নেমে পড়। এটা মরণফাঁদ। রহমান।’ রহমান হাসপাতালের বিছানা থেকে মধুমালার কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে বলে ওঠেন। মায়ের হাত গলিয়ে ট্রেন থেকে নেমে পড়ে রহমান। মধুমালার দিকে ছুটে যাওয়ার আগমুহূর্তে ট্রেনের ভেতর মাকে শেষবারের মতোন দেখার জন্যে ফিরে তাকায়; দেখে মায়ের নিবিড় বন্ধনে বসে আছে অন্য এক রহমান। হুবহু সে যেন। তার মুখে মিটমিট করে জ¦লছে এক রহস্যময় হাসি। শায়লা কাঁদতে কাঁদতে রহামানের সেই হাসিমাখা মুখে নিজের মুখ লাগিয়ে শেষবারের মতোন আলিঙ্গন করেন।