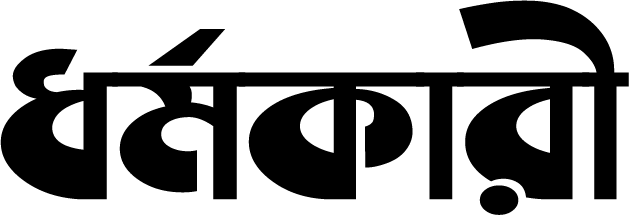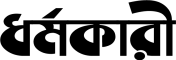মেঘমল্লার দেখে এলাম। টরন্টো ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের শেষ দিন ছিল সেপ্টেম্বর মাসে বিশ তারিখ। আর সেদিনই ছিল মেঘমল্লারেরও শেষ প্রদর্শনী। এই প্রদর্শনীটি ছিল টরন্টো ডাউনটাউনের ছিল স্কশিয়া ব্যাংক থিয়েটারে। এই ধরনের ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে বাংলা সিনেমা দেখা আমার জন্য দ্বিতীয়বার এটি। এর আগে দুই হাজার ছয় সালে ক্যালগারি ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে দেখেছিলাম ঋতুপর্ণ ঘোষের সাদা-কালোয় নির্মিত অসাধারণ চলচ্চিত্র ‘দোসর’।
বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের যে দৈন্যদশা বর্তমানে, সে কারণে এ ধরনের বিখ্যাত চলচ্চিত্র উৎসবে বাংলাদেশের ছবি সাধারণত আসে না। টরন্টো ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে মেঘমল্লার আসছে শুনে, আগে থেকেই মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছিলাম ছবিটি দেখবো বলে।
ফেস্টিভ্যাল শুরু হবার পরপরই মেঘমল্লার শেষ শো এর টিকেট বুক করে রেখেছিলাম অনলাইনে। শোর দিনে আমি আর আমার স্ত্রী গিয়ে হাজির হই স্কশিয়া ব্যাংক থিয়েটারে। মেঘমল্লারের শো ছিলো দুইটা পনেরোতে। দেড়টার সময় পৌঁছে গিয়েছিলাম আমরা। আন্ডারগ্রাউন্ডে গাড়ি পার্ক করে উপরে এসে বক্স অফিসের দিকে যেতেই মুক্তমনার লেখক শামান সাত্ত্বিকের সাথে দেখা। তিনিও সস্ত্রীক মেঘমল্লার দেখতে এসেছেন। উনারা আমাদের সামান্য আগে এসেছেন। বক্স অফিস থেকে টিকেট নিয়ে বাইরের দিকে কোথাও যাচ্ছেন। তাঁদের সাথে সৌজন্য কথা বলে আমরাও পা বাড়ালাম বক্স অফিসের দিকে। উদ্দেশ্য টিকেট সংগ্রহ করা। টিকেট সংগ্রহের পর দুজনে গিয়েছিলাম কিছু খেয়ে নেবার জন্য।
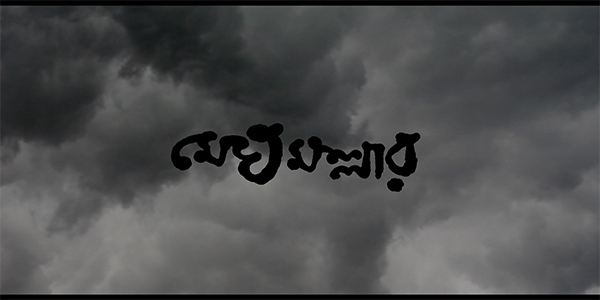
এই খেতে গিয়েই বিপদটা হলো। কিছুটা হেঁটে গিয়ে একটা টিম হর্টনস পেলাম। কিন্তু বিশাল লাইন। খাবার হাতে পেতে দীর্ঘ সময় লেগে গেলো। দুইটা বেজে গেছে প্রায়। হুমহাম করে স্যান্ডউইচ পেটে চালান দিয়ে কফি কাপ হাতে ছুট লাগালাম দুজনে থিয়েটারের দিকে। আপ টাউনের মানুষ আমরা, ডাউন টাউনের এমন ভিড়ে অভ্যস্ত নই। সেই ভিড় ঠেলে রীতিমতো দৌড়চ্ছি তখন আমরা। আমি রাগে গজগজ করছি, আমার স্ত্রী ঠাণ্ডা মাথায় আছে। আমার সব রাগ তার উপরে। আমি ব্যক্তিগত জীবনে সবসময়ই লেটে লতিফ, কিন্তু আজ মনে হচ্ছে যে ওই দায়ী। সে কারণেই রাগে ফুঁসছি। ওকে পিছনে ফেলে রেখে আমি এগিয়ে গিয়েছি। থিয়েটারের কোণায় এসে বাঁ দিকে বাক নিতে গিয়েই এক লোকের সাথে প্রচণ্ড ধাক্কা লাগলো। সামলে নিয়ে স্যরি বলতে গিয়ে দেখি ধাক্কাটা শামান সাত্ত্বিককে মেরেছি। তিনিও আমার মতো বউকে পিছনে ফেলে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছেন মেঘমল্লার দেখার জন্য। সিনেমা দেখা বড় দায়। বউয়ের খবর কে রাখে হায়? তারও আমার মতোই একই দশা। খাবার খেতে গিয়েছিলেন। আর সে কারণেই এই দেরি।
হলের মধ্যে ঢুকে দেখি পুরো হল ভর্তি মানুষ। শুধু সামনের কয়টা সারির সীট খালি আছে। এগুলো বাংলাদেশের সিনেমা হলের থার্ড ক্লাসের মতো। এখানে বসলে সিনেমা দেখতে হয় আকাশের দিকে মুখ করে। বাঁ দিকে, কিছুটা উপরে একটা সারিতে দেখি কয়েকটা সিট খালি আছে। দুজনে তড়িঘড়ি করে ওখানে গিয়ে দেখলাম যে সবগুলোর পিঠেই রিজার্ভড লেখা রয়েছে। এর মধ্যে দেখি ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল কর্তৃপক্ষের একজন শেতাঙ্গ মহিলা, চশমা পরা একজন ছোটখাটো দাড়িওয়ালা লোককে এনে সেই রিজার্ভ সীটে খুব খাতির করে বসাচ্ছে। বাকি তিনটা সীটে অন্য কেউ নেই। ভদ্রলোককে বাংলাদেশি বলেই মনে হলো। তাঁকে অনুরোধ জানাতেই তিনি বললেন, যে এখানে বসতে পারেন, আমার আর কেউ নেই। ভদ্রলোকের পাশে বসতে গিয়ে হুট করেই মনে হলো যে, এনাকে তো চেনা চেনা লাগছে। পত্রিকায় ছবি দেখেছি। জিজ্ঞেস করলাম যে, ‘আপনি এই ছবির পরিচালক অঞ্জন সাহেব না?’ উনি লাজুক হাসি দিয়ে বলেন যে, হ্যাঁ। তাঁর পাশে বসতে বসতে ভাবলাম, একেই বলেই সৌভাগ্য। একটু আগে বসারই জায়গা পাচ্ছিলাম না হলে, আর এখন ছবির পরিচালকের পাশে বসেই তাঁর সৃষ্টিকর্ম উপভোগ করতে যাচ্ছি।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ছোটগল্প রেইনকোট অবলম্বনে নির্মিত হয়েছে মেঘমল্লার। মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে নির্মিত এই ছবি। মাত্র তিন দিনের কাহিনি বিবৃত হয়েছে এখানে। সেই তিন দিনও আবার প্রচণ্ড বর্ষণমুখর তিনটি দিন। একজন নিরীহ গোবেচারা কলেজ শিক্ষক আর তাঁর পরিবারই মুখ্য এখানে। অত্যন্ত ভীতু ধরনের একজন মানুষ তিনি। ঘরের মধ্যে লুকিয়ে স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রের অনুষ্ঠান শুনতেও যার মন এ ভয় জাগে। রেডিওর কথা সহকর্মীকে বলে দেওয়াইয় স্ত্রীকে সামান্য ভর্ৎসনাও করেন তিনি। এরকম একজন ভিতু মানুষকে কলেজের ট্রান্সফর্মার উড়িয়ে দেবার ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্টতা আছে বলে বাসা থেকে কলেজে ডাকিয়ে নিয়ে যায় পাকিস্তান আর্মি। সেখান থেকে গ্রেফতার করে চোখ বেঁধে নিয়ে যায় তাদের ক্যাম্পে। তারপর চলে কথা আদায়ের জন্য অমানুষিক নির্যাতন এবং অবশেষে পাকিস্তান আর্মির ক্রুদ্ধ মেজরের গুলিতে মৃত্যু হয় তাঁর। বাসা থেকে যখন তাঁকে ডাকিয়ে নেওয়া হয় প্রবল বর্ষণে ভেসে যাচ্ছে বাইরের প্রকৃতি। তাঁর মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেওয়া শ্যালক মিন্টু ভুল করে বাসায় ফেলে রেখে গিয়েছিল তার রেইনকোট। সেই রেইনকোট গায়ে দিয়েই কলেজের দিকে যাত্রা করেছিলেন তিনি। ওটা গায়ে দেবার কারণেই হয়তো রূপান্তর ঘটেছিল তাঁর। অন্তত আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের গল্পে সেরকমই ইঙ্গিত আছে। যদিও চলচ্চিত্রে সেই বিষয়টা পরিষ্কার করে বোঝা যায় না। তবে, যে কারণেই হোক না কেনো, রূপান্তর ঘটে তাঁর। ভীত সন্ত্রস্ত একজন গৃহবাসী মানুষ থেকে দুঃসাহসী এক দেশপ্রেমিকে পরিণত হন তিনি। মাথা উঁচু করে স্বীকারোক্তি দেন যে, যারা ট্রান্সফর্মার উড়িয়েছে তাঁদের সবাইকে চেনেন তিনি, তারা সবাই তার ভাই-বন্ধু, সবকিছুই জানেন তিনি। কিন্তু একটা কথাও তিনি বলবেন না পাকিস্তান আর্মিকে। মরবার আগে বারবার দৃপ্তকণ্ঠে জয় বাংলা বলে যান তিনি।
মেঘমল্লার মুক্তিযুদ্ধের গল্প। মিন্টু এবং তার গেরিলা বন্ধুদের দেখানো হয় ছবির নানা দৃশ্যে। বিভিন্ন অপারেশনের পরিকল্পনা করে তারা। সেগুলোতে অংশও নেয়। উড়িয়ে দেয় ব্রীজ, ধ্বংস করে পাকিস্তান আর্মির জীপ, হত্যা করে সৈন্যদের। এতে তাদের সহযোদ্ধার মৃত্যুও হয়। কিন্তু কোনও অপারেশনকেই দেখানো হয় না ছবিতে। যেমন দেখানো হয় না পাকিস্তানি বাহিনীর নারকীয় হত্যাযজ্ঞ বা ধ্বংসযজ্ঞকে। সরাসরি কিছু না বলে, প্রত্যক্ষভাবে কিছু না দেখিয়েই সব বলে দেবার বা সব দেখিয়ে দেবার দারুণ এক মুনশিয়ানা এই ছবিতে দেখিয়েছেন পরিচালক। সিনেমার শেষে উনাকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম বিষয়টা নিয়ে। মুক্তিযোদ্ধাদের চুড়ান্ত একশন না দেখানোটা সচেতনভাবেই করা হয়েছে কিনা? উনি উত্তরে হ্যাঁ বাচক বলেছেন। হয়তো একারণেই মুক্তিযুদ্ধের ছবি হবার পরেও এখানে বারুদের ঝাঁঝালোতা চোখে লাগে নি, নাকে আসে নি পোড়ামাটির তীব্র গন্ধ। তার পরিবর্তে এসেছে মেঘ, বৃষ্টি, জল আর কোমল সবুজের কাব্যময়তা। হিংস্র একটা সময়কে, ধ্বংস, মৃত্যু, প্রতিরোধ আর পাল্টা লড়াইয়ের তীব্র কঠিন এক রুক্ষ্ণ বাস্তবতাকে কবিতার স্নিগ্ধতা দিয়ে মায়াময়ভাবে প্রকাশ করেছেন তিনি। এতে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ ম্লান হয় নি এতোটুকুও, মর্যাদা কমেনি এর সামান্যতমও। কোথাও হীন হয় নি এর সুউচ্চ অবস্থান। বরং দর্শকের হৃদয়ে ভিন্ন আবেশ নিয়ে লিরিক্যাল এক ছন্দে ধরা দিয়েছে তা।

মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা ঘটনা। বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের যাত্রা মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করেই শুরু হয়েছে। তবে, সেই যাত্রা যে পুরোটাই আবেগসর্বস্ব, সে কথা বলা যাবে না। মুক্তিযুদ্ধকে পুঁজি করে পয়সা কামানোর ধান্ধাতেও অনেকেই মুক্তিযুদ্ধের ছবি নির্মাণ করেছেন। সদ্য স্বাধীন দেশে মুক্তিযুদ্ধ নামের তীব্র আবেগের কারণে শুরুর দিকের প্রায় সব চলচ্চিত্রগুলোতেই মুক্তিযুদ্ধ এসেছে প্রবলভাবে, নির্মিত হয়েছে প্রামান্য চিত্র। সেগুলোতে প্রচারণারই বাহুল্য, শিল্পের অপার সৌন্দর্য সেখানে অনুপস্থিত। কড়া লাইনের, খাড়া লাইনের কবিতার মতো মুক্তিযুদ্ধ এসেছে চলচ্চিত্রে তখন। এর বাঁকশোভিত কোমল নন্দনতত্ত্ব তখন ছিল অনুপস্থিত। প্রথম সেই নান্দনিকতা নিয়ে আসেন আলমগীর কবীর তাঁর ধীরে বহে মেঘনা ছবির মাধ্যমে। তারপর তৈরি হয়েছে মেঘের অনেক রং। এতো ব্যাপক বিস্তৃত মুক্তিযুদ্ধ থাকার পরেও, সেই মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে বিশ্বমানের কোনো ছবি আমরা তৈরি করতে পারি নি। অনেকেরই একটা বড় ক্ষোভের জায়গা হচ্ছে যে, আমাদের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে পূর্ণাঙ্গ কোনো চলচ্চিত্র এখনও তৈরি হয় নি। এই পূর্ণাঙ্গ চলচ্চিত্রের বিষয়ে অবশ্য আপত্তি ছিল তারেক মাসুদের। তিনি তাঁর চলচ্চিত্রযাত্রা বইয়ের মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্র, চলচ্চিত্রের মুক্তিযুদ্ধ প্রবন্ধে লিখেছেন যে, “আমাদের অনেকের মধ্যেই একটি খেদ লক্ষ্য করার মতো বিষয় তা হচ্ছে, এত বছর হয়ে গেল মুক্তিযুদ্ধের ওপর একটি পূর্ণাঙ্গ চলচ্চিত্র আজও হলো না। আমরা যখন ‘পূর্ণাঙ্গ’ কথাটি ব্যবহার করি, তখন পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধের ছবি বোঝাই। কেবল যুদ্ধের ছবি কি মুক্তিযুদ্ধের পূর্ণাঙ্গ দিক? মুক্তিসংগ্রামের পূর্ণাঙ্গ দিক কি একটি ছবিতে আনা সম ভব অথবা খুবই দরকার? যুদ্ধ কেবল ওরা ১১ জনই করেনি, তাই বলে কেন ওরা ১১ জন এর যুদ্ধ সবার যুদ্ধকে প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না? মুক্তিযুদ্ধের রূপ ও রং এক নয়, যেমন মেঘের অনেক রং। মূল প্রসঙ্গের বাইরে মুক্তিযুদ্ধের এই যে হাজার রঙের দিক, হাজার অনুসঙ্গ, তার কত ক্ষুদ্র অংশই না আমরা ছবিতে আনতে পেরেছি! আমাদের প্রতিটি ছবি যদি মুক্তিযুদ্ধের একটি অনালোকিত প্রান্তিক দিক তুলে আনত, তা হলেই কি সব মিলিয়ে মুক্তিযুদ্ধের একটি যথাযথ পূর্ণাঙ্গ চিত্র ফুটে উঠত না? কাজটা প্রামাণ্যচিত্রের বেলায়ও ঘটে। কারণ, যেখানে নিউজ রিলের কাজ শেষ হয়, সেখানে প্রামাণ্যচিত্রের ভূমিকা শুরু হয়।“
এই অনালোকিত প্রান্তিক দিকই তুলে আনা হয়েছে মেঘমল্লারে। মুক্তিযুদ্ধের গ্রান্ড ন্যারাটিভ এখানে আসে নি। ইচ্ছা করেই আনা হয় নি। এসেছে ক্ষুদ্র একটা অংশ। একটা নিরীহ মধ্যবিত্ত পরিবারের চোখ দিয়ে মুক্তিযুদ্ধকে দেখানো হয়েছে এখানে। এই দেখা হয়তো মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের জন্য খণ্ডিত পঠন, কিন্তু চলচ্চিত্রের নান্দনিকতা, শিল্প মাধুর্যের জন্য অপার এক সুযোগ। সেই সুযোগ নিয়ে মেঘমল্লার মুক্তিযুদ্ধের প্রচার- প্রপাগান্ডার বাইরে গিয়ে হয়ে উঠেছে গভীরভাবে শিল্পোত্তীর্ণ এবং রসোত্তীর্ণ।
ছবিটার সবচেয়ে ভালো লেগেছে কী? অতি অবশ্যই এর সিনেম্যাটোগ্রাফি এবং আবহ সঙ্গীত। এটা বলার আগে বলে নেই যে চলচ্চিত্র বিষয়ে আমার কোনো পড়াশোনা নেই। কাজেই, এই ছবির ক্ষেত্রে আমার ভালো লাগা বা মন্দ লাগাটা পুরোটাই আমার চোখ এবং মনের ভালো লাগা, মন্দ লাগার সাথে সম্পর্কযুক্ত। আমার এই ভালো লাগার সঙ্গে অনেকেরই দ্বিমত থাকতে পারে, থাকাটাই স্বাভাবিক। অনেকে বিতর্কেও নেমে যেতে পারেন দ্বিমত করে, এই আশংকাও মাথায় থাকছে। মৃণাল সেন তাঁর ‘চলচ্চিত্রঃ ভূত-বর্তমান- ভবিষ্যৎ’ বইতে উল্লেখ করেছেন যে, ‘ছবি কতটা উতরোল কতটা উতরোল না, এ নিয়ে বিতর্ক চলবেই। চলাই উচিত। মতাদর্শের বিরোধ যেখানে অনুপস্থিত, সেখানে অনিবার্যভাবেই একটা অচলাবস্থা তৈরি হয় এবং সেটা কোনওভাবেই কাম্য নয়। দেখতে দেখতেই তৈরি হবে ছবি তৈরির বোল, ভাবতে ভাবতে সৃষ্টি হবে শিল্প সৃষ্টির মন, ভাঙতে ভাঙতেই গড়ে উঠবে নতুন মূল্যবোধের স্বাদ। অনেক আলোচনা-সমালোচনা, অনেক বিতর্ক কুতর্ক চলবে। চলুক। কোনটা শিল্প, কোনটা শিল্প নয়, এ নিয়ে নানা মুনির নানা মতকে উপেক্ষা করে লাভ নেই। এসব থেকেই তৈরি হবে শিল্পসম্মত ছবি এবং শিল্পবিচারের Objective দৃষ্টিভঙ্গি।‘সঙ্গীতেও কোনো জ্ঞান নেই আমার, তাই এ বিষয়ে বিস্তারিততে যাচ্ছি না। কিন্তু, সেই অজ্ঞানতাতেও অন্তত এটুকু টের পেয়েছি যে, প্রতিটা দৃশ্যের সাথেই এর আবহ সঙ্গীত গিয়েছে একই ঐক্যতানে, দুজনে দুজনার হয়ে।
ছবিটার সেরা কাজ আমার কাছে মনে হয়েছে এর ক্যামেরার কাজ। যে কোনো চলচ্চিত্রেই সবচেয়ে কঠিন কাজ হচ্ছে বৃষ্টির দৃশ্যকে ক্যামেরাবন্দি করা। আসল বৃষ্টি ক্যামেরায় ঠিকমতো আসে। লো বাজেটের ছবিতে কৃত্রিম বৃষ্টি তৈরি করাও পরিচালকের জন্য অনেক সময় সম্ভবপর হয় না। এ ছাড়া আরো নানা টেকনিক্যাল এবং অন্যান্য অসুবিধাতো রয়েছে। এই ছবির পুরো কাহিনিই ঘন বরষণের মাঝে। ছবির শুরু থেকে শেষ পর্যন্তই তাই বৃষ্টি দেখাতে হয়েছে পরিচালককে। এই দুরুহ কাজটা তিনি কীভাবে করেছেন, জানি না। বাংলাদেশের বর্ষার তুমুল বর্ষণকে তিনি শুধু সেলুলয়েডের পর্দায় বিশ্বাসযোগ্যভাবে তুলেই আনেন নি, বৃষ্টি, মেঘমালা, জল আর সিক্ত কোমল সবুজ দিয়ে অনিন্দ্যসুন্দর কাব্য রচনা করেছেন তিনি পুরো সিনেমা জুড়ে। এমন দৃশ্যকাব্য বাংলাদেশের সিনেমায় বিরল। চোখ আর চিত্তের জন্য বড়ই মনোহর তা, বড়ই মনোমুগ্ধকর। শো শেষ হবার পরে প্রশ্নোত্তর পর্বেও তাই পরিচালকের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল এ সম্পর্কে। এই বৃষ্টির কতোটুকু আসল আর কতোটুকু নকল ছিল। পরিচালক নির্দিষ্ট পরিমাণটা বলেন নি, শুধু বলেছেন যে, আসল আর নকলের মিশ্রণ এটি। আমার মূল লক্ষ্য ছিল আমাদের বর্ষাকে, বৃষ্টিকে বিশ্বাসযোগ্যভাবে ফুটিয়ে তোলা, তার জন্য যা করার তাই করেছি আমি সীমিত বাজেটের মধ্য দিয়ে। তবে, এই সিনেমা করতে গিয়ে এটাই যে তাঁর নিজের, ক্রুদের এবং অভিনেতা-অভিনেত্রীদের জন্য সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং কাজ ছিল, সেটা বলতে ভুল করেন নি তিনি।
যে সিনেমা হলে মেঘমল্লার দেখানো হয়েছিলো, সেটি ছিল বেশ বড়সড় সিনেমা হলই। এর পুরোটা ভরে গিয়েছিল সেদিন। শুধু সেদিন নয়, জাহিদুর রহিম অঞ্জন আমাকে জানিয়েছেন যে, মেঘমল্লারের প্রতিটা শো-ই এমন জনাকীর্ণ ছিল। আমি যেদিন দেখেছি, সেদিন দর্শকদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন অবাংলাদেশী। এরা গভীর আগ্রহ নিয়ে বাংলাদেশের সিনেমা দেখছে, সিনেমার পরে নানা ধরনের কৌতুহলী প্রশ্ন করছে ছবি দেখার প্রবল তৃপ্তি নিয়ে, এটা দেখাটা একজন বাংলাদেশি হিসাবে আমার জন্য বিরাট গর্ব এবং অহংকারের বিষয় ছিল।
এই ছবির ক্ষেত্রে আমার অবশ্য আনন্দ, গর্ব আর আবেগের আরো বড় একটা জিনিস রয়েছে। ছবিটার পুরো শুটিং করা হয়েছে ময়মনসিংহের বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে। এই ক্যাম্পাসে চাকুরিসূত্রে নয় বছর থেকেছি আমি। পর্দায় অনেক ভালবাসার চেনা পথ, চেনা বাড়ি, চেনা নদী, চেনা কাশবন দেখার আনন্দই অন্যরকম।
মেঘমল্লারের মতো কাব্যসুধাময়, শিল্পমাধুর্যপূর্ণ, অনিন্দ্যসুন্দর চলচ্চিত্র আরো অনেক তৈরি হোক, সেই কামনাই রইলো।